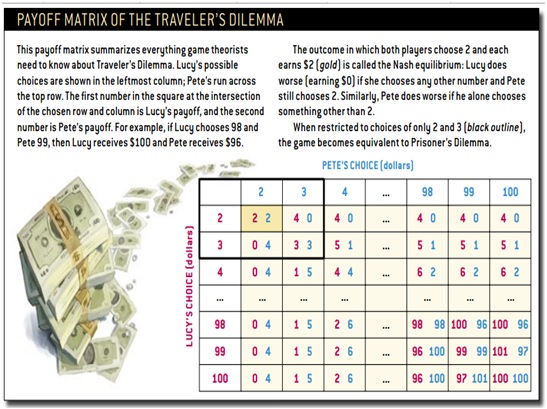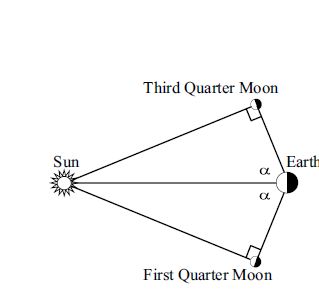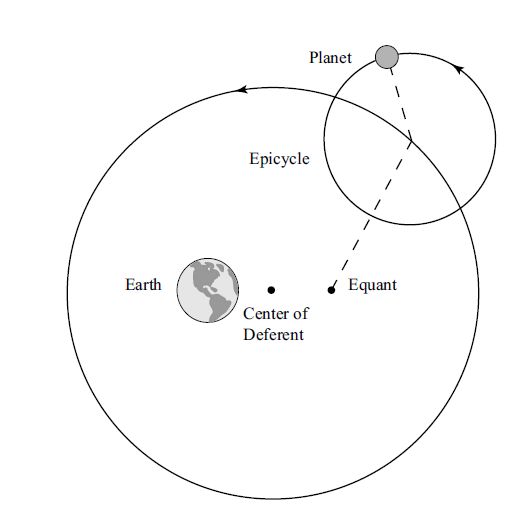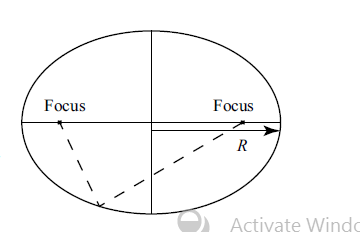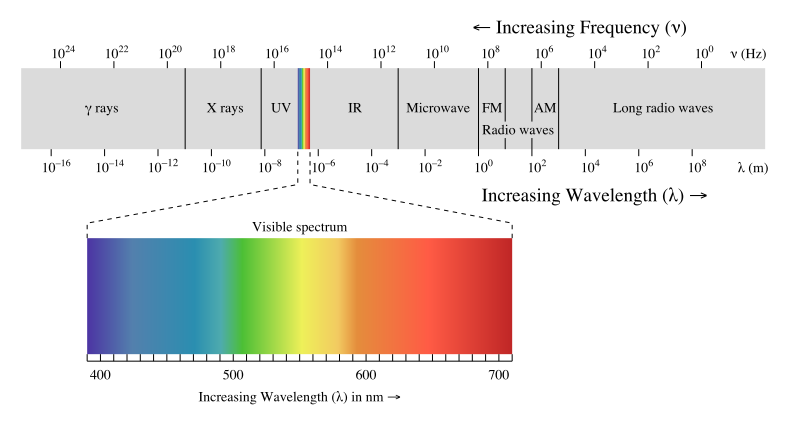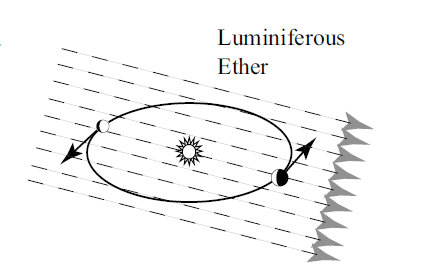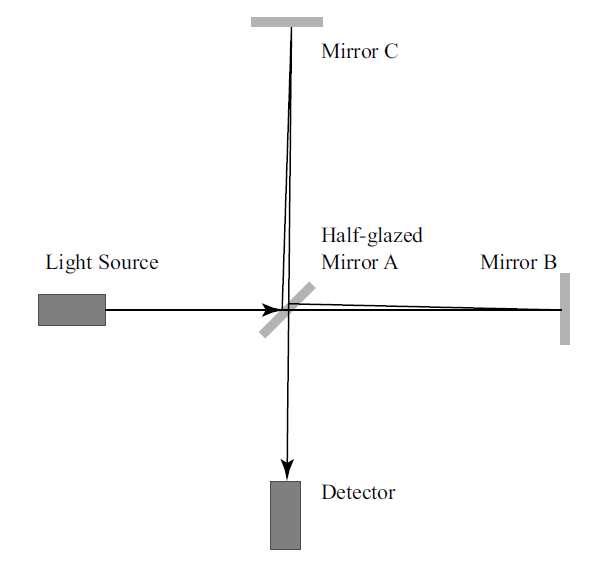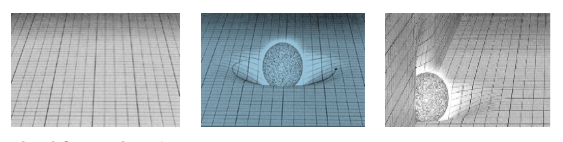বানিজ্যিক যৌনতার কেনা-বেচায় সুইডেন প্রথম দেশ হিসাবে, ক্রেতাকে অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করে, বিক্রেতাকে নয়।
ইংরাজি ‘সেক্স ট্রেড’ এর বাংলা কি হতে পারে? যৌনতার বানিজ্য? হয়তো এমন কিছু একটা। ভারতীয় উপমহাদেশে আমরা এর নাম দিয়েছি ‘পতিতাবৃত্তি’। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এখানে অর্থের বিনিময়ে যৌনকর্মের শুধু একজন অংশীদারকেই যুক্ত করা হচ্ছে, বাকিজন যিনি খরিদ্দার তাকে এক রকমের সোস্যাল ইনডেমনিটি বা সামাজিক সুরক্ষা দেয়া হচ্ছে। এটাই পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্র অর্থের বিনিময়ে নারীকে যৌনতা বিক্রি করতে বাধ্য করে এবং দিনের শেষে সেই কর্মটির জন্যে তাকেই “পতিতা” হিসাবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বিক্রির পেশাটিতে শুধু সেই “পতিতা”রই দায় থাকে; তাই পেশাটির নাম “পতিতাবৃত্তি”। এই ‘পতিতাবৃত্তি’ নামকরনের ব্যাখ্যা অনেক নারীবাদী লেখক দিয়েছেন। আমি নীতিগতভাবে ‘পতিতাবৃত্তি’ লিখিনা, বলিনা। তাই আমি একে বলছি ‘যৌনতার বানিজ্য’। এই বানিজ্যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমানভাবে উপস্থিত।
এখন শিরোনামে যে বিতর্কের কথা লিখেছি তা খুব সাধারণ, সাদামাটা। এটা একটা ঔচিত্যবোধের প্রশ্ন। প্রশ্নটা করেই ফেলি আগে, তারপরে এই প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্কগুলো ব্যাখ্যা করা যাবেঃ
“পেশা হিসাবে বানিজ্যিক ভাবে যৌনতার কেনাবেচা কি থাকা উচিৎ”? আর এই কেনাবেচার বাজার বলে আমরা যা জানি অর্থাৎ ব্রোথেল বা পতিতালয় কি থাকা উচিৎ?দুটি প্রশ্নে শেষে “উচিৎ” শব্দটি দিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, এই প্রশ্নের হাজারটা উত্তর হতে পারে। এটা নির্ভর করবে ব্যক্তি মানুষ হিসাবে, সমাজ হিসাবে আমার বা আমাদের “ঔচিত্যবোধ” এর উপরে। মুশকিল হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ঔচিত্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন। এটা কেবলই একটি পার্থক্য বা ভিন্নমত। ধরুন, এই প্রশ্নটি যদি ইউরোপের সভ্য দুটি দেশ নেদারল্যান্ডস ও জার্মানিতে করা হয়, তাহলে হয়তো প্রশ্নকারীর দিকেই বিস্ময়কর চোখ দিয়ে তাকাবেন অন্যান্য মানুষেরা। কেননা, নেদারল্যান্ডস বা জার্মানিতে যৌনতার বানিজ্য শুধু বৈধই নয়, এটা একটা স্বীকৃত পেশা, যারা আরো দশটা পেশার মতোই রাষ্ট্রকে আয়কর দিয়ে নিজের পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ জার্মানি কিংবা নেদারল্যান্ডসে মৌলিক অর্থে একজন ডাক্তার, অধ্যাপক, ট্রাকচালক কিংবা একজন যৌনকর্মীর মাঝে পেশাগত সংজ্ঞার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই । হয়তো সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে এখনো, কিন্তু এঁরা সবাই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত পেশায় নিয়োজিত এবং সবাই আয়কর দেয়া মানুষ, তাই আয়করের সুবিধা হিসাবে সকল সামাজিক কল্যাণের সমান অধিকার ভোগ করে থাকেন।
এমন কি সংরক্ষণবাদী পাঠকদের হয়তো ভালো লাগবেনা পড়তে, তবুও বলি, নেদারল্যান্ডস বা জার্মানিতে এই পেশাটির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হয়তো যৎকিঞ্চিত পার্থক্য আছে, তবে তা আরো দশটি পেশার চাইতে খুব খারাপ কিছু নয়। নেদারল্যান্ডস এ বানিজ্যিক যৌনকর্মীরা স্কুলে বা কলেজে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে পারেন- কেনো একজন যৌনকর্মী হওয়াটা আরো দশটা পেশার মতোই একটি সাধারণ পেশা। বরং স্বাধীনতার দিক থেকে কেনো এই পেশাটি একটি কাংখিত পেশা হতে পারে।
এই তথ্যগুলো উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বলা যে, বানিজ্যিকভাবে যৌনতা বেচা-কেনার পেশা থাকা উচিৎ কিনা- এই বিষয়টি দারুণভাবে নির্ভর করে একটি সমাজের গড় মূল্যবোধের উপরে, আর সেই মূল্যবোধের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আইনের উপরে। এবং সভ্যতার নিরিখে অনেক সমাজ আছে যাদেরকে আমরা সভ্য ও মানবিক সমাজ বলে মনে করি, তারা মনে করেন বানিজ্যিকভাবে যৌনতা বেচাকেনার মাঝে কোনো নীতিগত সমস্যা নেই। যেমন ধরা যাক, জার্মানি বা নেদারল্যান্ডস এ জনমত হচ্ছে, নারী বা পুরুষের যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। গণতন্ত্র ও সারা বিশ্বের মানবতার প্রধান ঠিকাদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যের মাঝে মাত্র একটিতে যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচা বৈধ, আর বাকি উনপঞ্চাশটি রাজ্যে যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচা নিষিদ্ধ। যদিও বাস্তব পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যেই যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচার অবাধ বানিজ্য বিদ্যমান।
যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচার প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে নারী হচ্ছেন বিক্রেতা আর পুরুষ ক্রেতা। দুই একটি দেশ বাদ দিয়ে, প্রায় সত্তুর – আশি শতাংশ নারী এই পেশায় আসেন হয় “মানব পাচার” বা হিউম্যান ট্র্যাফিকিং এর শিকার হয়ে, নয়তো চরম দারিদ্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে। যেহেতু মানব পাচার এবং তার পরবর্তী বাধ্যতামূলক যৌনদাসত্ব এভাবেই চক্রটি শুরু হয় ও চলতে থাকে, তাই এখানেই একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কেউ কেউ, – এই পেশাটি কেনো নারীর বিরুদ্ধে একটি পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়ন নয়? সারা বিশ্বে আসলে ঠিক কতজন নারী সত্যিকার অর্থেই নিজের ইচ্ছায় আরো দশটি পেশার মতো করেই “বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রির” পেশা বেছে নেন? কোনো সন্দেহ নেই, এই প্রশ্নগুলো জটিল।আজ থেকে প্রায় আঠারো বছর আগে, ১৯৯৯ সালে সুইডেন প্রথম ঘুম ভাঙ্গালো সারা বিশ্বের। সুইডেন ঘোষণা করলো, যৌনতা বিক্রি কোনো অপরাধ নয়, কিন্তু যৌনতা খরিদ করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ, টাকা বা ভিন্ন কিছুর বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলো দেশটিতে। সারা বিশ্বে সম্ভবত যৌনতা বিষয়ে সবচাইতে খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গির দেশ হচ্ছে সুইডেন। এখানে ছেলে মেয়েরা খুব ছোট বয়স থেকেই যৌনতা ও মানুষের যৌন সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, স্কুলের পাঠ্যসূচীতে প্রাতিষ্ঠানিক যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয় খুব ছোটবেলা থেকেই। মানুষের যৌনতা সম্পর্কে, তা সে নর-নারী, নর-নর কিংবা নারী-নারীতে হোক না কেনো, মানুষের পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্ক বা সাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই দেশটির মতো উদার দেশ শুধু ইউরোপে নয়, সারা বিশ্বেই খুব কম আছে। সেই রকমের একটি সমাজে হঠাৎ করে “যৌনতার বানিজ্য” বন্ধ করে দেয়াটা ছিলো এক ধরনের বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত। শুধু সুইডেনের নয় সারা বিশ্বের পিতৃতন্ত্র হামলে পড়েছিলো এই সিদ্ধান্তের উপরে।
সুইডেনের এই নতুন আইনটির পেছনে রাজনীতি, নারীবাদী দর্শন ও সুইডেনের সামাজিক মূল্যবোধ কাজ করেছে। কিন্তু সহজভাবে, অর্থনীতির ভাষায় এটাকে বলে চাহিদার জায়গাটিকে নিরুৎসাহিত করা। আমাদের সমাজে এরকমের বহু উদাহরণ আছে। যেমন, সিগারেট উৎপাদনকে নিষিদ্ধ না করে, বরং সিগারেটের উপরে অতি উচ্চ করারোপ এবং ধুমপানের বয়স আইন করে নির্ধারণ করে দেয়া। কিংবা এলকোহল উৎপাদনকে নিষিদ্ধ না করে বরং মদ্যপানের ন্যূনতম বয়স আইন করে নির্ধারণ করে দেয়া। ঠিক তেমনি, বানিজ্যিকভাবে যৌনতা কেনার খরিদ্দার ৯০% ক্ষেত্র পুরুষ এবং এই বানিজ্যের ফলে নারীর উপরে নিপীড়নের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাই সুইডেনে এই আইনের মধ্যে দিয়ে মূলত পুরুষের এবং পুরুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে। এটা ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের পিতৃতন্ত্রের গালে একটা বিরাট চপোটাঘাত।
কিন্তু ঠিক কি কি নীতিগত বিতর্ক তৈরী করেছিলো সুইডেনের এই সিদ্ধান্তটি? ফেসবুকে যে নারীবাদী লেখক একাই ভিন্ন স্রোতের একটি মন্তব্য করে সবার বিরাগভাজন হয়েছিলেন, মূলত তাঁর মতো করেই প্রশ্নটিই করেছেন এবং এখনও করছেন অনেক গবেষক, নারীবাদী, মানবতাবাদী, রাজনীতিবিদসহ আরো অনেকেই। ইউরোপে সেই একই প্রশ্ন নিয়ে অনেকেই একাডেমিক গবেষণা করছেন, কেউ তাঁদের গালিগালাজ করে কোণঠাসা করছেন না। সেই প্রশ্নগুলো সেই বিতর্কগুলো তুলে ধরাই এই লেখার উদ্দেশ্য।
২.
যৌনতা বিক্রি অপরাধ নয়, ক্রয় করাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই দারুণ বিতর্কিত আইনটি প্রথম প্রনয়ণ করে সুইডেন এবং পরবর্তীতে নরওয়ে ও আইসল্যান্ড এবং সাম্প্রতিক সময়ে ক্যানাডা এবং ফ্রান্সও একই রকমের আইন প্রনয়ণ করে। একটি নরডিক দেশ সুইডেন এই আইনের প্রথম প্রবক্তা বলে এই মডেলটির নাম হয়ে যায় “নরডিক মডেল”। নরডিক মডেল সারা সুইডেন ও ইউরোপেতো বটেই সারা বিশ্বেই আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়। নারীবাদী, সাধারণ জনগণ, রাজনীতিবিদ, একাডেমিক সমাজতাত্ত্বিকবৃন্দসহ প্রায় সকল শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়েন এই ইস্যুতে। খোদ সুইডেনেই, আইনটির বিপক্ষে মত দিয়েছিলো প্রায় ৭০ শতাংশ নাগরিক (জনমতে অংশগ্রহণকারীর ৭০ শতাংশ), সুইডিশ জাতীয় সংসদ বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো, এমনকি দ্বিমত পোষণ করেছিলো আইন পেশার বিশেষজ্ঞরা, আদলত ও বিচারকেরা, পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্তাব্যক্তিরাও।
৩.
প্রখ্যাত আমূল নারীবাদী (র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট) গবেষক ও লেখক, অধ্যাপক ক্যাথরিন ম্যাককিনন তাঁর এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন –
“আর্থসামাজিক অসমতা দূর করতে হবে এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই, মানব পাচার বা হিউম্যান ট্র্যাফিকিং বন্ধ করা দরকার, এটা নিয়েও কেউ কখনও দ্বিমত করেছেন বলে শুনিনি। কিন্তু “যৌনতার বানিজ্য” বা প্রস্টিটিউশন বন্ধ করা দরকার, এই ইস্যুতে সচেতন মানুষদের অনেকেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। অনেকেই মনে করেন, বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে সঠিক বা “পলিটিক্যালি কারেক্ট”, সুতরাং কি দরকার এই ইস্যুতে নিরর্থক খোঁচাখুচি করার”।অধ্যাপক ম্যাককিনন এর পর্যবেক্ষণের বাস্তবতা আছে, পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে নানান রকমের আন্দোলন, সংগ্রাম গড়ে উঠেছে গত একশো বছরে, সেখানে আজও নারীকে তাঁর নিজের শরীর বিক্রি করে জীবন ধারণের জন্যে অর্থ উপার্জন করতে হয় এবং এই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে খুব বেশী একটা আলোচনা নেই। আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সারা বিশ্বে, মানব পাচার, বানিজ্যিক যৌনতা ও পর্ণগ্রাফী ব্যবসার মোট বাজার এর তথ্য বিস্ময়করভাবে প্রমাণ করে, এটা আজকের আধুনিক পুঁজিবাদের পরম স্নেহে লালিত-পালিত একটা বানিজ্যিক ধারা। চরম অমানবিক কিন্তু দারুণ লাভজনক। কে না জানে, টাকার কোনো ধর্ম নেই, উচিৎ-অনুচিৎ বোধও নেই। তাইতো পুঁজিবাদী সমাজের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ এই পেশাটিকে টিকিয়ে রাখার স্বপক্ষে অনেক যৌক্তিক অবস্থান তৈরী করেছে।
এই প্রশ্নটি নিয়ে নারীবাদীদের মাঝেও রয়েছে মতামতের সুস্পষ্ট বিভক্তি। বানিজ্যিকভাবে নারীর যৌনতা বিক্রিকে নারীবাদীরা কিভাবে দেখে থাকেন? এর উত্তরে বলা যায়, প্রস্টিটিউশন বা যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচা প্রসঙ্গে, আধুনিক সময়ে, পশ্চিমা নারীবাদীরা অন্তত তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত। এদের কে সহজ বাঙলায় বলা যেতে পারে-
১ – কঠোর বা নির্মূলপন্থী (Strict or Abolitionist feminist)কঠোর বা নির্মূলপন্থীরা মনে করেন, যৌনতার বানিজ্য হচ্ছে নারীর প্রতি পিতৃতন্ত্রের আরেকটি শোষণমূলক ব্যবস্থা।- এটা আংশিক নয় বরং সম্পূর্ণ বিলোপ হওয়া উচিৎ। উদারনীতিবাদীরা মনে করেন, নারী যদি চায় তাহলে তিনি তাঁর শরীর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারেন, এবং এইজন্যে তাকে নির্যাতিত বা ভিক্টিম হিসাবে চিহ্নিত করাটা অনুচিৎ। কেননা একজন নারীর শরীর সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজের, সুতরাং তাঁর নিজের শরীর নিয়ে তিনি কি করবেন তা নিয়ে কারো কিছু বলার নেই, এমন কি রাষ্ট্রেরও কিছু বলার নেই। আর প্রজ্ঞাবান বা প্র্যাগমাটিস্ট ফেমিনিস্টরা মনে করেন, নৈতিকভাবে এই বিষয়টি যেমনই হোক না কেনো, যৌনতা বিক্রি বা কেনা, কোনটাই প্রচলিত অর্থে অপরাধ হওয়া উচিৎ নয়। এই তিন দলের নারীবাদীরা যৌনতার কেনা-বেচার প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্কে বেশ সরব। এছাড়াও আরো দুই গোত্রের নীরব নারীবাদীরা আছেন যারা মনে করেন, এই পেশাটি চলতে পারে, তবে এই পেশার ফলে নারীর উপরে যত নিপীড়নমূলক আচরণ আছে তা নির্মূল করতে হবে। এই শেষ গোত্রের নারীবাদীরা মনে করেন, কোনটা স্বেচ্ছায় বেছে নেয়া আর কোনটা বাধ্যতামূলক যৌনদাসত্ব- সেই বিষয়টি খুব পরিস্কার করে সংজ্ঞায়িত করা দরকার এবং স্বেচ্ছা নির্ধারিত পেশা হিসাবে একে সুরক্ষা দেয়া ও বাধ্যমূলক যৌনদাসত্বকে নির্মূল করা উচিৎ।
২ – উদারনীতিবাদী (Liberal Feminist)
৩ – প্রজ্ঞাবান (Pragmatic feminist)
৩.
একটি আধুনিক পুঁজিবাদী দেশ হয়েও কেনো প্রায় সকল দেশ ও সমাজ থেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে সুইডেন এই রকমের একটি সিদ্ধান্ত নিতে গেলো? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে সুইডেনের এই আইনের ইতিহাসটি সংক্ষেপে জানা দরকার।
যৌনতার কেনা-বেচা প্রসঙ্গে কঠোর বা নির্মূলপন্থীদের প্রথম দিকের উদাহরণ হচ্ছে সুইডিশ আমূল নারীবাদী বা র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা। সুইডেনের সরকারী উদ্যোগে দুই দফায় বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হয়, প্রথমবার ১৯৮২ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৩ সালে। সরকারী উদ্যোগে নেয়া এই গবেষণাধর্মী অনুসন্ধানে সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ অংশ নেন এবং গবেষণা দলের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন একজন নারী।
এ প্রসঙ্গে এই আইন প্রনয়ণের গবেষণা কাজের একজন প্রধান গবেষক Cecilie Høigård বলেছিলেন –
সুইডেনের এই আইন তৈরীর করার আগে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক গবেষণা ও জরিপ করেছি। আমরা বানিজ্যিক যৌন কর্মীদের সাথে বছরের পর বছর মিশেছি, কথা বলেছি, তাঁদেরকে জানার চেষ্টা করেছি। আমাদেরকে অনেক বানিজ্যিক যৌনকর্মী বলেছেন যৌনকর্ম বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বোধের কথা। বানিজ্যিক যৌনকর্মীদের কেউ কেউ বলেছেন –প্রশ্নটি নিয়ে আধুনিক কালের নারীবাদীরা বিভক্ত হয়ে গেছেন। বিশেষ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ফেমিনিস্ট মতামত এই আইনের বিপক্ষে গেছে। তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। “আমার শরীর, আমার সিদ্ধান্ত” এই মতামতে বিশ্বাসীদের অনেকেই এই আইনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এটা নারীর শরীর নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত নেবার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করবে। অনেকেই বলেছেন, বানিজ্যিক যৌনকর্ম একটি পেশা বা কাজ, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টিয়ে এই পেশাকে সম্মানজনক পেশার মর্যাদা দেয়া দরকার। পাশাপাশি এই আইনটির স্বপক্ষের মানুষেরা বিতর্ক তুলেছেন, বানিজ্যিক যৌনকর্ম কোনো পেশা নয়। তাঁরা দাবী করেছেন, সকল পেশাই একটি নির্দিষ্ট দক্ষতার দাবী করে এবং সকল পেশাই মানুষকে ক্ষমতাবান বা এম্পাওয়ারড করে তোলে, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে। কিন্তু বানিজ্যিক যৌনকর্মীদের বেলায় দেখা যায়- শুধুমাত্র এই পেশায় থাকার কারণে তাঁরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন পড়েন। ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার বদলে তাঁরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, এই নারী কর্মীদের উপরে নেমে আসে অর্থের বিনিময়ে “বৈধ” নিপীড়নের সন্ত্রাস। শেষোক্ত যুক্তিতে বানিজ্যিক যৌনকর্মকে সুইডেনে কোনো “পেশা” বা “বৃত্তি” হিসাবে স্বীকার তো করা হয়ইনি, বরং মনে করা হয়েছে- এটা নারীর বিরুদ্ধে যৌনতা নির্ভর আর্থ-সামাজিক অসমতাকে টিকিয়ে রাখে এবং যা এক ধরনের শোষণই বটে। বলা হয়ে থাকে, সারা বিশ্বের বিরুদ্ধ স্রোতে গিয়ে এই রকমের একটি ব্যাখ্যা ও রাজনৈতিক অবস্থান নেয়ার মূল কারণ ছিলো, সুইডেনের সেই সময়কার ক্ষমতাসীন সরকারে বামপন্থী, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট আর আমূল নারীবাদীদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য।
“বানিজ্যিকভাবে যৌনকর্মের এই পেশাটিতে কাজ করার সময় আমার নিজের যোনীকে অনেকটা রেন্টাল এপার্টমেন্ট এর মতো মনে হয়। প্রতিদিন কিংবা কিছুদিন অন্তর অন্তর একজন অচেনা মানুষ এসে এপার্টমেন্টটি ব্যবহার করে যান টাকার বিনিময়ে। যৌনকর্মের মতো কাজটিতে মনোদৈহিক অংশগ্রহণ দরকার হয়, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে নিজের শরীর থেকে মনকে আলাদা করতে হয়। কেননা মন এই অজানা মানুষটিকে গ্রহণ করতে পারেনা, কিন্তু শরীরকে এদের গ্রহণ করতে হয় টাকার জন্যে”।
কিন্তু এই আইন একই সাথে বেশ কিছু জটিলতা ও স্ববিরোধীতা তৈরী করেছিলো। কিছু জটিলতা একেবারে নিরেট রাষ্ট্রীয় আর কিছু জটিলতা নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর মানবাধিকার প্রশ্নে।
বানিজ্যিক
যৌনতা বিক্রির বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের বিধি নিষেধ আরোপের প্রচেষ্টাকে
যৌনকর্মীদের অধিকার খর্ব করার শামিল বলে মনে করেন একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক
অধিরকার কর্মী ও নারীবাদী মানুষ।
৪.
প্রথম স্ববিরোধীতাঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবাধিকার যৌনতা বিক্রি করা অপরাধ নয়, কিন্তু খরিদ করা দন্ডনীয় অপরাধ, এই আইনটি প্রথম যে স্ববিরোধীতাটি তৈরী করেছিলো তা হচ্ছে, নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন পছন্দ বা “ফ্রি চয়েস”, এবং মানবাধিকার বিষয়ক প্রশ্নের মাঝে বিরোধ। এই বিষয়গুলোতে সারা বিশ্বব্যাপী একই মানদন্ড বজায় রাখার জন্যে কখনও আন্তর্জাতিক ঘোষণাসমূহ (যেমন জাতিসংঘের) ঘোষণা আবার কখনোবা স্থানীয় আইন বা উভয়ই ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, তিনটি আন্তর্জাতিক ঘোষণায় মানুষের যে সমস্ত অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়েছে, তা সুইডিশ এই বিশেষ আইনটির ক্ষেত্রে এসে স্ববিরোধী অবস্থানে মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। এই তিনটি ঘোষণা হলোঃ
1. International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights to Self Determination (ICESCR)যেমন ধরা যাক, প্রথম ঘোষণাটি বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। অর্থাৎ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন। মানুষের এই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারের ক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্র কোনো বাঁধা তৈরী করতে পারবে না। এই ঘোষণার অধীনে মানুষের প্রাপ্ত অধিকারটিকে অনেক সময় “ফ্রি চয়েস” বা “ফ্রি উইল” বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। যারা যৌনতা কেনা-বেচার “নরডিক মডেল” এর বিরোধিতা করেন, তাঁরা ICESCR ঘোষণাকে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে নরডিক মডেল মানুষের “ফ্রি চয়েস” বা স্বাধীনভাবে পেশা বা বৃত্তি বেছে নেবার অধিকারকে হরণ করে। যৌনকর্মীদের স্বাধীনভাবে পেশা বেছে নেবার অধিকারকে খর্ব করেছে “নরডিক মডেল”, অথচ স্বাধীনভাবে নিজের পেশা বা বৃত্তি বেছে নেবার অধিকার একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার। অন্যদিকে এর বিপরীতে CEDAW ঘোষণা আন্তর্জাতিকভাবে সকল নারীকে যেকোনো ধরনের নির্যাতন ও নিবর্তনমূলক পরিস্থিতি থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। CEDAW ঘোষণা নারীকে যে কোনো ধরনের যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত রাখার নিশ্চয়তা দাবী করে এবং খোদ নারীর জন্যেই যেকোনো ধরনের বানিজ্যিক বা বাধ্যতামূলক যৌনতা বিক্রির পেশা ত্যাগ করার অধিকার প্রদান করে। জাতিসংঘের সকল ঘোষণার মাঝে একমাত্র CEDAW ঘোষণাতেই ইংরাজিতে ”Prostitution” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে ভিন্ন আরেকটি শব্দকে নিয়ে। যেভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হয়েছে CEDAW ঘোষণাতে, তার নানান ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। CEDAW ঘোষণাতে এই বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে –
2. International Covenant on Civil and Political rights (ICCPR)
3. Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
“Right to be free from exploitation of prostitution (CEDAW, Article 6)”এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সকল prostitution কি exploitation বা শোষণমূলক? এ বিষয়ে বিভক্তি দেখা গেছে দেশে দেশে, রাজনীতিবিদদের মাঝে, নারীবাদীদের মাঝে এমনকি মানবতাবাদীদের মাঝেও। কেউ কেউ মনে করেন, prostitution সকল ক্ষেত্রে শোষণমূলক নাও হতে পারে। যদি যথাযথভাবে “মানব পাচার” কে প্রতিহত করা যায় এবং forced slavery বা বাধ্যতামূলক দাসত্বকে প্রতিহত করা যায় তাহলে prostitution সকল ক্ষেত্রে শোষণমূলক নাও হতে পারে। এবং রাষ্ট্র যদি এই পেশাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হয় তাহলে এই পেশার মাঝে নিবর্তন বা শোষণমূলক ঘটনাগুলোকে কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে prostitution বা বানিজ্যিক যৌনতা কেনা-বেচার পেশাটি নারীর জন্যে শোষণমূলক নাও হতে পারে। ঠিক এই যুক্তিটিতেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশের সাথে এমনকি সারা বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের সাথে সুইডেন ও নরডিক দেশগুলোর প্রধান পার্থক্য। সুইডিশ সরকার এবং এখানকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে, পৃথিবীর সকল ধরনের prostitution বা বানিজ্যিক যৌনতার কেনা-বেচার ঘটনা মূলত নারীর প্রতি নিবর্তনমূলক ও শোষণমূলক। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর প্রতি কোনো নির্যাতন বা শোষণের ঘটনা না ঘটলেও, সম্ভাবনার হার খুব উল্লেখযোগ্য। সুইডিশ আমূল নারীবাদীদের (Radical Feminist ) একাংশ যাদের নির্মূলবাদী বা Abolitionist feminist বলা হয়ে থাকে, তারা মনে করেন, সকল অর্থেই নারীর জন্যে বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রির পেশাটি অপমানজনক, নির্যাতনমূলক এবং এটা হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতনের একটি সুস্পষ্ট নজির। সুইডিশ গবেষণায় দেখা গেছে, বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রির কাজে অর্থের লেনদেন হলেও এটা সবসময়ই নারীর প্রতি এক ধরনের বল প্রয়োগের ঘটনার জন্ম দেয় আর বল প্রয়োগের স্থানে কেবল পুরুষই ভূমিকা রাখে (Florin, 2012)। নির্মূলপন্থী নারীবাদীরা হচ্ছেন আমূল নারীবাদীদের একটি অংশ। আমূল নারীবাদীরা ষাটের দশকে প্রথম ঘোষণা করেন, নারী–পুরুষের রোম্যান্টিক সম্পর্কও রাজনৈতিক, এর মাঝেও রয়েছে পিতৃতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক শোষণ, যেখানে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ হচ্ছে শোষকের ভুমিকায় (Saunders, 2005)। তাই আমূল নারীবাদীদের শ্লোগান ছিলো “Personal is political” অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিষয়ও রাজনীতির বাইরে নয়। সুইডিশ নারীবাদীদের এই অনড় অবস্থানের কারণেই মূলত আন্তর্জাতিক ঘোষণাগুলোর সাথে স্ববিরোধী অবস্থান সত্ত্বেও সুইডেনে এই আইনটি পাশ করা সম্ভব হয়েছিলো । সাম্প্রতিক জরিপগুলো বলছে, সুইডেনের প্রায় ৭০ ভাগ নাগরিক মনে করেন, এই আইনটি প্রত্যাশামাফিক কাজ করছে এবং এই আইনটি নারীর উপরে পুরুষের নির্যাতন কমিয়ে এনেছে এবং নারীর জন্যে একটি “অসম্মানজনক” বৃত্তির হার কমিয়ে আনছে। পুরুষের বানিজ্যিক যৌনতা কেনার হারও কমে এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে।
‘Free choice’ বা স্বাধীন পছন্দের অধিকার খর্ব করার প্রশ্নে সুইডিশ সরকার, ক্ষমতাসীন দল ও নারীবাদীদের পাল্টা যুক্তি হচ্ছে, ফ্রি চয়েস বা স্বাধীন পছন্দ নিশ্চিত করতে হলে মানুষকেও সত্যিকারের স্বাধীন করে দেয়া দরকার। অর্থাৎ, মানুষ বাধ্য হচ্ছে এমন যে কোনো অবস্থা দূর করার পরেই কেবল পরীক্ষা করা যেতে পারে, মানুষ আসলেই স্বাধীন পছন্দ হিসাবে বানিজ্যিক যৌনতাকে বেছে নিচ্ছে কিনা। অর্থাৎ, একজন নারীর ব্যক্তিগত দারিদ্র দূর করে, তার উপরে যেকোনো রকমের ভয়-ভীতি দূর করে, তারপরে তার সামনে যদি একই রকমের বেতন ও সুযোগ সুবিধার পাঁচটি চাকুরীর প্রস্তাব রাখা হয়, সেখান থেকে যদি কোনো নারী চারটিকে বাদ দিয়ে বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রির পেশাকে বেছে নেন, তাহলেই কেবল সেটাকে বলা যেতে পারে নারী তাঁর স্বাধীন পছন্দ হিসাবেই যৌনতা বিক্রির পেশা বেছে নিচ্ছেন। কিন্তু সুইডিশ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বেশীরভাগ নারীই যৌনতা বিক্রির পেশাকে বেছে নিচ্ছেন অন্য কোনো কাজ না পেয়েই, নয়তো দালালের খপ্পরে পড়ে কিংবা ইমিগ্র্যান্ট হিসাবে নতুন সমাজে এসে কোনো রকমের অর্থনৈতিক সমাধান খুঁজে না পেয়ে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য দালালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুইডিশ নারীবাদীদের মতে, স্বাধীন পছন্দ বা “ফ্রি চয়েস” এর যুক্তিটি এখানে একেবারেই প্রযোজ্য নয়।
৫.
দ্বিতীয় স্ববিরোধীতা – চাকুরীর বাজার ও সামাজিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া
দ্বিতীয় সমস্যাটি তৈরী হয় এই আইনের ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতি আইনের বিচার ভিন্ন হওয়া থেকে। এই আইনটিতে একজন নারী, পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ নিজের পেশা হিসাবে বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রেতা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করতে পারেন। এটাতে তাদের কোনো আইনী বাঁধা নেই। কিন্তু ক্রেতা হিসাবে সেই বাজারে আইনত কেউ উপস্থিত নেই, কারণ যৌনতা কেনা দণ্ডনীয় অপরাধ। সুতরাং এখানে পেশাদার যৌনতা বিক্রেতা আছেন কিন্তু তাদের কোনো বৈধ ক্রেতা নেই। যেহেতু তাদের কোনো বৈধ ক্রেতা নেই, তাই বাস্তবত তাদের কোনো আয়-রোজগার নেই। এই প্রশ্নে সুইডিশ ট্যাক্স অফিসের সাথে নারীবাদী ও ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জায়গাটি দুর্বল। সুইডিশ ট্যাক্স অফিস বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রিকে একটি পেশা বা কাজ মনে করেনা। কিন্তু যে কোনো নাগরিকের ঘোষিত আয় হচ্ছে করযোগ্য (অবশ্য একটি নির্দিষ্ট সীমার উপর থেকে প্রযোজ্য)। সুইডিশ ট্যাক্স অফিসের সাথে এটা একটা সরাসরি স্ববিরোধী অবস্থান যৌনতা বিক্রি বিষয়ক আইনের। আবার যখন একজন নারী বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রি থেকে আয়-রোজগার শুরু করেন, তাই ধরে নেয়া যায় তার নিজেকে ও পরিবারকে চালানোর জন্যে অর্থনৈতিক সাহায্য দরকার নেই। তাই সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তিনি আর বেকার ভাতা বা “সামাজিক কল্যাণ ভাতা” পাবার যোগ্যতা রাখেন না। একাধিক গবেষক দাবী করেছেন, এই স্ববিরোধ এর মূল শিকার হচ্ছেন নারী যৌনকর্মীরা যারা নিজেদের যৌনতা বিক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করার কারণে সুইডিশ সামাজিক কল্যাণ থেকে আংশিক বা উল্লেখযোগ্যভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন অথচ নিজেদের জীবন ধারণের জন্যে যথেষ্ট আয়ের সুযোগ নেই তাদের। তাই এই মানুষেরা নিশ্চিতভাবে সামাজিক অবহেলার শিকার হচ্ছেন। যৌনতার ক্রেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে যে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন যৌনকর্মীরা তার নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।
জার্মানি
ও নেদারল্যান্ড সহ ইউরোপের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশে “সেক্স ওয়ার্ক”
একটি বৈধ পেশা যা নরডিক দেশগুলোর মতামতের সরাসরি বিরোধী।
তৃতীয় স্ববিরোধীতা – সামাজিক কলংক, গোপনীয়তা ও নৈতিকতার প্রশ্ন
নরডিক মডেলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ক্রেতাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং সামাজিকভাবে যৌনতা ক্রেতাকে অধিক উন্মোচিত করা। ফলে ক্রেতা, যার প্রায় ৯৫% হচ্ছে পুরুষ, সামাজিক কলংকের ভয়ে যৌনতা কেনা থেকে বিরত থাকবেন। এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছে, অর্থাৎ, নরডিক সমাজে পুরুষের বানিজ্যিক যৌনকর্মীর কাছ থেকে যৌনতা কেনার হার অনেকাংশে কমে গেছে। কিন্তু এর ভিন্ন রকমের প্রভাব পড়েছে যৌনকর্মীদের উপরে, বিশেষত নারী যৌনকর্মীদের উপরে। যেহেতু প্রকাশ্যে যৌনতা কেনার সুযোগ নেই, তাই এর ক্রেতারা গোপনে যৌনতা কেনার শর্ত আরোপ করেন যৌনকর্মীদের উপরে এবং সেই গোপন বানিজ্যে নারীর প্রতি নিপীড়নের মাত্রা আরো বেশী হয় বলে গবেষণায় দেখা গেছে। চুড়ান্ত অর্থে গোপনে যৌনতা বিক্রির মন্দ প্রভাবের শিকার হচ্ছেন নারী যৌনকর্মীরা। গোপনে বানিজ্যিক যৌনতা বিক্রির জন্যে নারী যৌনকর্মীদেরকে নির্ভর করতে হয় দালালের উপরে। অনেক সময় এই দালালেরাই ব্যবস্থা করেন গোপন স্থান বা এপার্টমেন্টের। ফলে নানানভাবে, নারী যৌনকর্মীরা এক রকমের বন্দী জীবন যাপন করেন এই দালালদের হাতে। যদিও রাষ্ট্রীয় হিসাব মতে এই বন্দীত্বের শিকার নারীর সংখ্যা খুবই নগন্য, তবুও গবেষকেরা দাবী করেছেন এই খুব নগন্য সংখ্যক নারীর জীবনও ভয়াবহ হুমকীর মধ্যে থাকে সারা বছর। যেহেতু ক্রেতার সংখ্যা এখন একেবারেই কম, তাই অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে যৌনকর্মীদের দর কষাকষির ক্ষমতা বা বারগেইনিং পাওয়ার প্রায় নেই বললেই চলে, ফলে তারা বাজার মূল্যের চাইতে অনেক কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এখানেও যৌনতার ক্রেতাদের চাইতে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন যৌনকর্মীরা। ফলে সুইডেনের নারীবাদীদের সাথে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের যে আদর্শবাদী ঐক্য তার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশটির যৌনকর্মীরা । তারা প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কতটুকু নৈতিক যে নারীবাদীদের ও বামপন্থী ক্ষমতাসীন দলের আদর্শিক ঐক্যের কারণে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে একজন যৌনকর্মী ভুক্তভোগী হবেন?
নৈতিকতার প্রশ্নে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের নৈতিকতার মানদন্ড ঐতিহাসিকভাবেই খ্রিষ্টতান্ত্রিক ধর্মের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপরে নির্মিত। তাই এখানে এখনো সাধারণ জীবনযাত্রায় বা বানিজ্যিক যৌনতা বা Prostitution কে মনে করা হয় অনৈতিক পেশা বা অনৈতিক কর্ম। খ্রিষ্ট ধর্ম মতে সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যে নয় এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌন সঙ্গম সবসময়েই অনৈতিক। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, দারুণভাবে সেকুলার ও নিরীশ্বরবাদী সমাজ সুইডেনেও সরকারী নথিপত্রে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বানিজ্যিক যৌনকর্মীদের মানুষ হিসাবে মনে করা হতো অনৈতিক, অসৎ। অবশ্য, এখন নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রের কাছে একজন যৌনকর্মী সকল অর্থেই আর দশটা নাগরিকের মতোই সমান। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এখনো একজন যৌনকর্মীর অবস্থান আরো দশটি নাগরিকের মতো নয়।
অধিকার প্রসঙ্গে একাডেমিক গবেষকদের কেউ কেউ এই ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন (Dworkin, 2011: p.32-33)। এই সকল একাডেমিক গবেষকেরা ব্যাখ্যা করেন, অধিকার সব সময়ই “ব্যক্তিগত”। প্রতিটি মানুষ সমান অধিকার দাবী করেন। তাই একটি বিরাট অংশের “ক্ষতি” কমানোর জন্যে অন্য একটি সংখ্যালঘু অংশের ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব করাটা কতটুকু নৈতিক- সেই প্রশ্ন তুলেছেন এদের কেউ কেউ। অর্থাৎ একটা বৃহত্তর অংশের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে একটা ক্ষুদ্রতর অংশের ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করাটা কতটুকু নৈতিক? এই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।
৭.
চতুর্থ স্ববিরোধীতা – “বলির পাঁঠা” কে বা কারা হওয়া উচিৎ?
ইংরাজী শব্দ ”Victimhood” এর বাংলা অর্থ বলির পাঁঠা হয় কিনা আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু একদল গবেষক এই ”Victimhood” কে সামনে নিয়ে এসেছেন বানিজ্যিক যৌনতা কেনা-বেচার বিতর্কে। তারা প্রশ্ন তুলেছেন কেনো কেবল বানিজ্যিক যৌনকর্মীরাই বলির পাঁঠা বা ”Victimhood” এর শিকার হবেন (Jackson 2016)। সুইডিশ ফেমিনিস্টদের যুক্তির বিপরীতে এই গবেষকদের দাবী ও প্রশ্ন হচ্ছে – যদি বানিজ্যিক যৌনতা কেনা-বেচার মূল কারণ দারিদ্র্য, মানব পাচার, শৈশবের যৌন হয়রানী ও পিতৃতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক শোষণ হয়ে থাকে, তাহলে মূল কারণগুলো দূর করার উদ্যোগ নেয়াটাই তো প্রধান কর্মসূচী হওয়া দরকার এবং যদি এই কারণগুলোই নারীর উপরে এই আদিম নির্যাতনের মূল কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তো যৌক্তিকভাবে এই কারণগুলো দূর করলেই তো বানিজ্যিক যৌনতার বাজার শুন্য হয়ে আসবে। অর্থাৎ, দারিদ্র যদি প্রধান কারণ হয়ে থাকে নারীর জন্যে যৌনতার বানিজ্যে অংশগ্রহণের, তাহলে কোনটা প্রধান উপায় হতে পারে প্রতিরোধের, দারিদ্র বিমোচন নাকি আইন করে নারীকে তার অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ করে দেয়া? যদি হিউম্যান ট্রাফিকিং বা মানব পাচার একটি প্রধান কারণ হয়ে থাকে বানিজ্যিকভাবে যৌনতা কেনা-বেচার, তাহলে নারীর উপরে এই নিবর্তন বন্ধ করার উপায় কি হতে পারে? মানব পাচার বন্ধ করা নাকি আইন করে রাস্তার যৌনকর্মীদের রুটি রুজির উপরে খড়গ-হস্ত হওয়া? এখানে যুক্তি ও নৈতিকতা দুটো বিষয়ই কাজ করছে। সুইডিশ ফেমিনিস্টদের মতে “ডিম্যান্ড সাইড” বা চাহিদাকে নিরুৎসাহিত করতে পারলে সরবরাহ ও কমে যাবে আর অপর পক্ষের অনেকের মতে যদি সরবরাহ দিক বা সাপ্লাই সাইড প্রি-কন্ডিশনগুলোকে (দারিদ্র, মানব পাচার ইত্যাদি) বন্ধ করা যায় তাহলে ডিম্যান্ড বা চাহিদাও তৈরী হবেনা। দুপক্ষেরই উদ্দেশ্য একই, কিন্তু একপক্ষ যৌনকর্মীদের দুর্ভোগের সম্পূর্ণ বিপক্ষে, যৌনকর্মীদের ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে, অপর দিকে নির্মূলপন্থী নারীবাদীদের মতে আইন করেই এই নিপীড়নমূলক বানিজ্যিক প্রথা দূর করা যাবে, তাতে আপাত একটি সময়ের জন্যে হয়তো কিছু নারীর ভোগান্তি হবে, তবে দীর্ঘমেয়াদে তা নারীমুক্তি ও নারীর সমানাধিকারকেই নিশ্চিত করবে।
৮.
পঞ্চম স্ববিরোধীতাঃ বানিজ্যিক যৌনতা কেনার হার বনাম “সেক্স ট্যুরিজম”
এই লেখাটির জন্যে এই স্ববিরোধীতাটিই শেষ উল্লেখযোগ্য স্ববিরোধিতা। বাস্তব পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এই আইনটি কি আসলেই পুরুষের টাকা দিয়ে যৌনতা ক্রয় করাকে কমাতে পেরেছে? সুইডিশ জাতীয় পরিসংখ্যান বলছে, এই আইনের ফলে সুইডেনে টাকার বিনিময়ে যৌনতা কেনার হার কমেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। আমেরিকায় যেখানে প্রতি পাঁচ জনে একজন পুরুষ বছরে অন্তত একবার বানিজ্যিকভাবে যৌনতা কিনে থাকেন সেখানে সুইডেনে এই অনুপাতটি প্রতি ১১২ জনে একজন। এটা সন্দেহাতীতভাবেই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। কিন্তু অনেকেই এই পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা এই পরিসংখ্যান, সাম্প্রতিক সময়ের ক্রমবর্ধমান প্রপঞ্চ “সেক্সটুরিজম” কে অন্তর্ভুক্ত করেনা। সুইডিশ পুরুষদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিছু নির্দিষ্ট দেশে ভ্রমনের মাত্রা, যে দেশগুলোর খ্যাতি রয়েছে “সেক্স ট্যুরিজমের” জন্যে (থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, স্পেইন, ইউক্রেইন ইত্যাদি) । যদি এই সেক্স ট্যুরিজম এর হারকে সুইডিশ পরিসংখ্যানের অন্তর্গত করা হয়, তাহলে সত্যিকার অর্থে “নরডিক মডেল” এর প্রকৃত কার্যকারিতা বোঝা যেতে পারে। যা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অপরদিকে সুইডিশ আইন বা “নরডিক মডেল” প্রবাসে সুইডিশ নাগরিকের যৌনতা ক্রয় করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করেনা, যদি সেই দেশটিতে তা বেআইনি না হয়ে থাকে। ফলে, একটা বিপুল সংখ্যক সুইডিশ পুরুষ ভিন্ন দেশে গিয়ে যৌনতা খরিদ করছেন, নীতিগতভাবে যা অগ্রহণযোগ্য।
৯.
যৌনতার বেচা-কেনারঃ পক্ষ-বিপক্ষ
বলাই বাহুল্য, নরডিক মডেল এর পক্ষে ও বিপক্ষে সমানভাবে সারা বিশ্বব্যাপী আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের পরাক্রমশালী দেশগুলো এই আইনের তীব্র সমালোচনা করেছে এবং এখনো করছে। এই সমালোচকদের তালিকায় রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, নারীবাদী, মানবাধিকার কর্মীসহ সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষই আছেন। ক্যানাডা এবং ফ্রান্স সাম্প্রতিক সময়ে একই রকমের আইন পাস করেছে তাদের সংসদে। বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় দেশ ফ্রান্স এই আইন পাস করার পরে পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মাঝে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরী হয়েছে। মানব পাচার, ব্রোথেল এবং পর্ণোগ্রাফির ব্যবসার স্বপক্ষের শক্তিগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই আইনের বিরুদ্ধে। দুই পক্ষেরই রয়েছে নানান ধরনের যুক্তি পাল্টা যুক্তি। অনেক একাডেমিক গবেষক এই আইনকে নারীর আত্মমর্যাদাকর ভাবার বদলে বামপন্থিদের “ব্যর্থ দিবাস্বপ্নের” সাথে তুলনা করেছেন। অনেকেই মনে করছেন, নারীর সমানাধিকার তো দূরের কথা, এই আইনের একমাত্র ভুক্তভোগী হবে নারী।
৯.
সংক্ষেপে মূল বিতর্ক
নারীবাদীদের মূল যুক্তি
সুইডিশ ফেমিনিস্ট, ক্ষমতাসীন সোশ্যালডেমোক্র্যাট দল ও অন্যান্য বামপন্থী ও মধ্যপন্থী দলের মতে, বানিজ্যিক ভাবে যৌনতার কেনা-বেচার প্রথা আসলেঃ
১ – প্রস্টিটিউশন বা বানিজ্যিক ভাবে যৌনতা বিক্রি সকল অর্থেই নারীর উপরে পিতৃতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের আরেকটি ধরন।আমূল নারীবাদীদের যে অংশটি বানিজ্যিকভাবে যৌনতা বেচা-কেনা সম্পূর্ণ বন্ধ বা নির্মূল করতে চান, তাদের সর্বশেষ যুক্তিটি হচ্ছে – যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচা হচ্ছে বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রকরন যা প্রমাণ করে, “চাহিবা মাত্রই পুরুষের সেবা করতে নারী বাধ্য”। এই প্রথা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নারীর শরীর “বিক্রিযোগ্য” এবং তা কেবল পুরুষের সেবায় এবং যখনই দরকার, পুরুষ যেনো তা পায়, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। যে সমাজ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দর্শনে বিশ্বাসী, সেই সমাজে এই রকমের “অসমতা” শুধু অন্যায্য নয়, অমানবিক এবং আদিম। সুইডেন সমাজ হিসাবে এই অসমতা, অন্যায্যতা, অমানবিকতা ও আদিমতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেনা।
২ – এই নিপীড়নের একমাত্র শিকার নারী আর নীপিড়কের ভুমিকায় পুরুষ। বানিজ্যিকভাবে যৌনতা কেনা-বেচার সাথে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ধরনের কাজে অবধারিত ভাবেই নারী শারীরিক ও মানসিক ভাবে নির্যাতিত হয়।
৩ – বানিজ্যিক যৌনতা বেচা-কেনার সাথে সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশই পুরুষ, এরা প্রায়শই অপরাধী, কখনও মানব পাচারকারী, কখনোবা নিপীড়ক দালাল আবার কখনোবা ক্রেতা নামের ধর্ষক। এরা অপরাধী, এদের আইনী শাস্তির বিধান বৈধ।
৪ – যৌনকর্মীদের মাঝে “ফ্রি চয়েস” বা স্বাধীন ইচ্ছার চর্চার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হয় সত্যিকারের স্বাধীন ইচ্ছা গড়ে ওঠার অভাব অথবা যথেষ্ট সুযোগের অভাব এর কারণ। “ফ্রি চয়েস” বা “ফ্রি উইল” খর্ব হওয়া প্রসঙ্গে সুইডিশ নারীবাদীদের স্পষ্ট অবস্থান হচ্ছে, ফ্রি-চয়েস বা ফ্রি-উইল নিয়ে বিতর্কের আগে মানুষ সত্যিকারের অর্থে ফ্রি করে দিতে হবে। মানুষ তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানগতভাবে ফ্রি না হলে তার চয়েস বা নির্বাচন ফ্রি হতে পারেনা। অর্থাৎ মানুষের সামনে তার যোগ্যতা অনুযায়ী আরো পাঁচটি পেশা বেছে নেবার সুযোগ তৈরির সাথে যদি তার পক্ষে যৌনতা কেনা-বেচার “পেশা”কেও একটি পছন্দ হিসাবে রাখা হয় এবং যদি নারীর আরো চারটি পেশা গ্রহনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যৌনতা বিক্রির পেশাকে গ্রহণ করে, তাহলেই সেটাকে নারীর “ফ্রি চয়েস” হিসাবে বলা যাবে। বাস্তবতা তার প্রমাণ দেয়না।
৫ – মূলত মানব পাচার ও যৌনদাসত্ব একই ধরনের অপরাধ। দুটোরই উদ্দেশ্য একই। তাই যৌনদাসত্বকে চিরতরে দূর করতে হবে, তাহলে মানব পাচার এর মতো ঘৃণ্যতম অপরাধকে দূর করা সম্ভব।
৬ – বানিজ্যিকভাবে যৌনতা কেনা-বেচার এই ব্যবসা সাম্প্রতিক সময়ে এতোটাই ফুলে ফেপে উঠেছে যে এর সাথে যুক্ত হয়েছে মানব পাচারের এক বিরাট গোপন বানিজ্য। এটা একটা বড়সড় সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যাকে দূর করতে হবে।
৭ – বানিজ্যিক যৌনতার কেনা-বেচাকে আইনত বৈধ ঘোষণা কেবল নারীর অবস্থানকেই আরো খারাপ করে তুলবে, বিশ্বব্যাপী মানব পাচারকে আরো বৃদ্ধি করবে যার একমাত্র পরিনতি হচ্ছে নারীর উপরে পুরুষের নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি।
৮ – প্রস্টিটিউশন বা বানিজ্যিক যৌনকর্ম কোনো পেশা হতে পারেনা, কেননা এই পেশা মানুষকে বিশেষত নারীকে শক্তিমান করার বদলে বিচ্ছিন্ন করে, নারীর জীবন ও নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করে এবং সামাজিকভাবে এই পেশা কোনো “মূল্য” উৎপাদন করেনা।
যৌন কর্মীদের পক্ষের মূল যুক্তি
১ – যৌনতার বানিজ্যিক কেনা-বেচা বন্ধের এই আইন, মানুষের মৌলিক ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ। এটা আধুনিক রাষ্ট্রের এক ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক খবরদারী।
২ – এটা যৌনকর্মীদের মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
৩ – এই আইন, যৌন কর্মীদেরকে “ভুক্তভোগী”তে পরিনত করেছে। তাদেরকে বাধ্য করেছে অস্বাভাবিক, গোপন জীবন যাপনে। এর ফলে সমাজের কাছ থেকে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের যে ন্যায্য “কল্যাণ” পাবার যে অধিকার তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। পদ্ধতিগতভাবে যৌনকর্মীদেরকে সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। যা অমানবিক।
৪ – এই আইন যৌনকর্মীদেরকে আরো বেশী করে সামাজিক “কলংক”র মুখোমুখি করে তুলেছে। বহু বছর ধরে চলে আসা ধারণা যে যৌন কর্মীরা পাপী, মন্দ মানুষ, নীতিগতভাবে তারা স্ত্রী হতে পারেন না, মা হতে পারেন না, এই সকল নারী-বিরুদ্ধ ধারণাকেই আরো বদ্ধমূল করে তুলেছে।
৫ – এই আইন যৌনকর্মীদের উপরে অত্যাচার না কমিয়ে বরং আরো অনেক বেশী বৃদ্ধি করবে, কারণ এখন ক্রেতা অনেক শক্তিমান এবং বিক্রেতা হিসাবে নারীকে যেহেতু অনেক গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়, তাই তার উপরে শারীরিক জুলুমের আশংকা এখন আরো অনেক বেশী।
৬ – যৌনতা বেচা-কেনা একটি পেশা অথচ সুইডেন এই পেশার নিরাপত্তা দিতে পারছে না। পেশার নিরাপত্তা দেয়ার বদলে তারা পেশাটিকেই “নিষিদ্ধ” করছে, এটা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
৭ – এই আইনটি মানুষের “স্বাধীন ইচ্ছা”র সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
শেষ কথা
এই সমগ্র লেখাটির প্রেরণা ছিলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম “ফেসবুক” এর একটি বিতর্ক। যে বিতর্কে বাংলাদেশের আত্মদাবীকৃত নারীবাদীদের সকলেই একমত ছিলেন “বেশ্যাবৃত্তি” থাকা উচিৎ কিনা- এই প্রশ্নে। কেবল একজন উল্লেখ করেছিলেন, তিনি মনে করেন “বেশ্যাবৃত্তি” থাকা উচিৎ নয়, কিন্তু কেউ যদি নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এই পেশায় যুক্ত হতে চায়, তাহলে তার আপত্তি নেই। ব্যস, আর যায় কোথায়, বাকী সকলে মিলে তাকে কোণঠাসা করে ফেললেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ, গালিগালাজে তাকে সন্ত্রস্থ করে তুললেন এবং অবধারিত পরিণতি হিসাবে ব্যক্তিগত গালাগালি দিয়ে শেষ হলো সেই বিতর্কটি। যদিও, এই একই রকমের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিতর্কটি চলছে বহু বছর ধরে, গালাগালি ছাড়াই, দারুন গঠনমূলকভাবে, সেখানে ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, নীতিশাস্ত্র সকল প্রেক্ষিত নিয়ে বিতর্কটি এগিয়ে চলেছে। এই বিতর্কের এখনো কোনো কূল কিনারা হয়নি। সম্ভবত এই বিতর্ক চলবে আরো বহু বছর, এর মধ্যে দিয়েই মানুষ আরো মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করবে। সেখানে হয়তো বাঙালি হিসাবে আমাদের অবদান খুব সামান্যই থাকবে, কেননা আমরা আমাদের সময়গুলো ব্যয় করেছি ও করবো গালাগালিতে।
এই লেখাতে ব্যবহৃত সকল উৎসই ইংরাজী ও সুইডিশ ভাষার। কিন্তু এই লেখাটির পেছনে আমার প্রায় দুই সপ্তাহের পরিশ্রমের মূল কারণ হচ্ছে, এই বিতর্কটিকে বাংলা ভাষায় পরিচয় করিয়ে দেয়া। লেখার কোথাও আমি আমার নিজের মতামত ব্যক্ত করিনি, কারণ আমি শুধু এই আন্তর্জাতিক বিতর্কটিকে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষপাত সুইডিশ আমূল নারীবাদীদের মতের স্বপক্ষে, কিন্তু আমি মনে করি, এই আইনটির বিপক্ষে যারা কথা বলছেন, তাদের অনেক মতামতের পেছনে যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে যা ভবিষ্যতে সমাধান করতেই হবে।
আমি প্রত্যাশা করি, আগামীতে এই বিষয়ে আরো সৃজনশীল বিতর্ক আমরা দেখবো বাংলা ভাষায়।
বিশেষ নোটঃ এই লেখাটির প্রথম অংশ, ভুমিকার অংশটুকু ভিন্ন একটি ব্লগ সাইটে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু দুই একটি নীতিগত কারণে আমি এই লেখাটি সেই ব্লগ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি মনে করি এই লেখাটি মুক্তমনার পাঠকদের জন্যে আরো অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহউদ্দীপক হবে। আশা করি মুক্তমনার পাঠকেরা লেখাটি উপভোগ করবেন।
যে সকল সুত্রের সাহায্য নিয়েছি এই লেখাটি লিখতেঃ
প্রকাশিত জার্নাল প্রবন্ধ – নিবন্ধ – রিপোর্ট সমুহঃ
Dworkin R (2011), Rights as trumps, Philosophy of human rights, 1st Ed. Westview press
Edwards S (1997), The legal regulation of prostitution: A human rights issue, Routledge, London
Gould A (2001), The criminalization of buying sex: the politics of prostitution in Sweden, J of Soc. Pol, 30 (3), p. 437 – 456
Green K (1989), Prostitution, exploitation and taboo, Philosophy, 64, p.525 – 34
Ekberg G (2004), The Swedish law that prohibits the purchase of a sexual service: Best practices for prevention of prostitution and trafficking in human beings, Violence against women, 2004, 10, p. 1187 – 1218
Florin O (2012), A particular kind of violence: Swedish social policy puzzles of a multipurpose criminal law, Sex Res Soc Policy, 9.3, p.269 – 278
Jackson CA (2016), Framing sex-worker rights: How US sex worker rights activists perceive and respond to mainstream anti-sex trafficking advocacy, Sociological Perspective, 59.1, p. 27 – 45
NSWP, The real impact of the Swedish model on sex workers, Edinburgh, Global Network of Sex work project, 2015
Saunders P (2005), Traffic violations: Determining the meaning of violence in sexual trafficking versus sex work, Journal of interpersonal violence, 20.3, p.343 – 360
অনলাইন সুত্রঃ
https://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-paternalistic-fallacy_b_9644972.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/08/criminsalise-buying-not-selling-sex
http://edition.cnn.com/2016/04/18/opinions/prostitution-nordic-model-peters/index.html